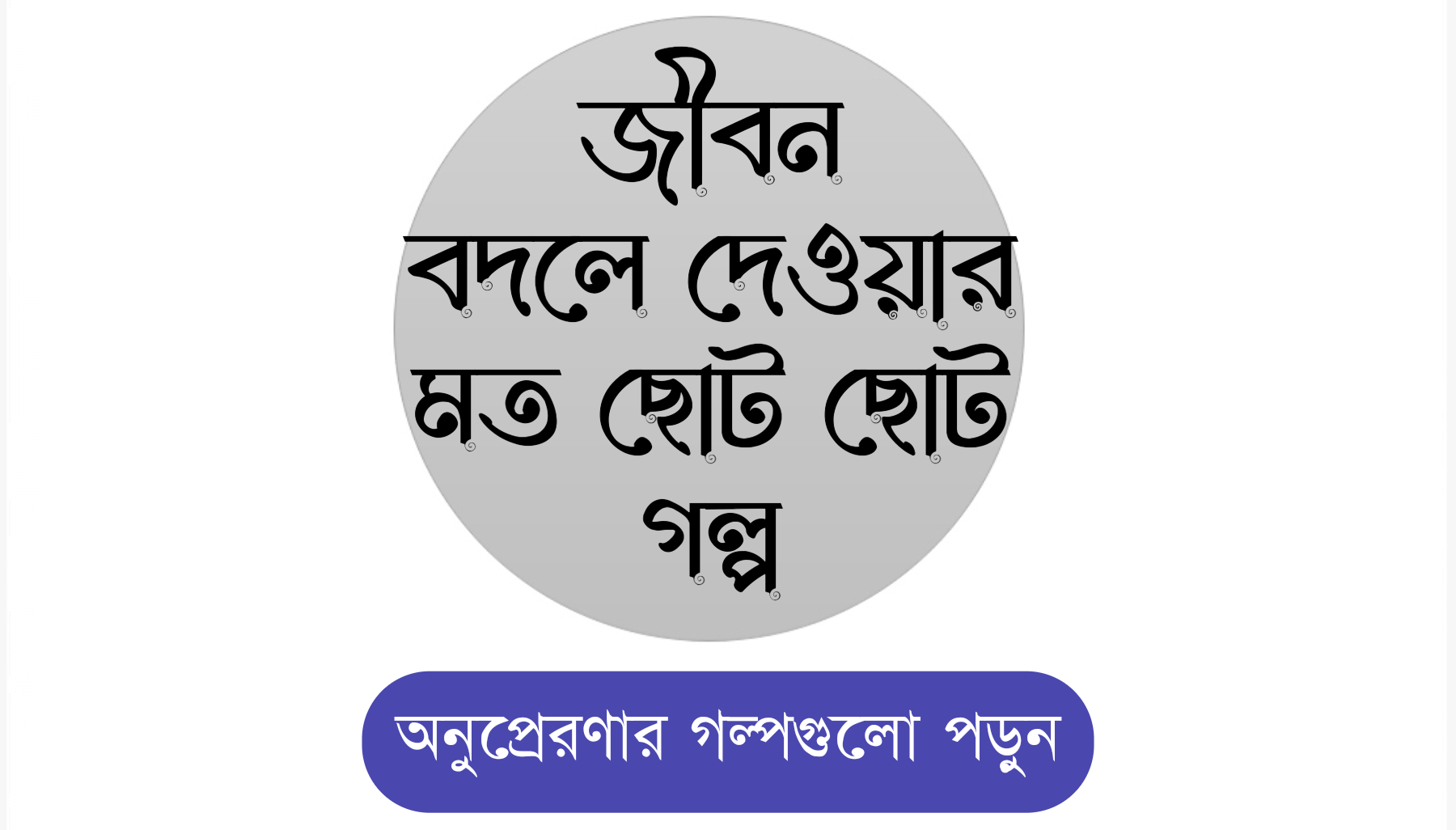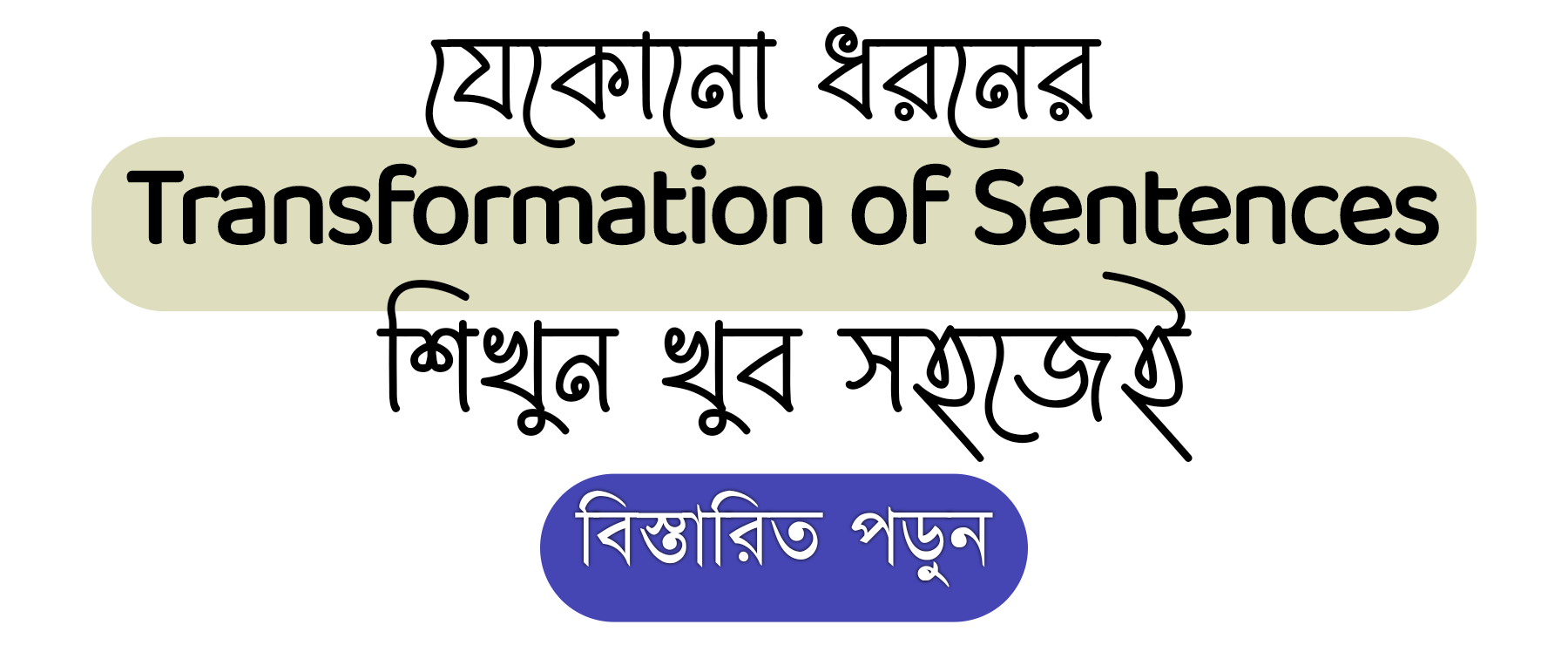বিসিএস লিখিত + ভাইভা
সত্তরের নির্বাচন ও বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক দূরদর্শিতা
১৯৭০ সালের ডিসেম্বরে পাকিস্তানের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো অনুষ্ঠিত হয় ‘এক ব্যক্তি এক ভোট’ নীতির ভিত্তিতে সর্বপাকিস্তান সাধারণ নির্বাচন। স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে যে দেশ প্রতিষ্ঠা পেল ১৯৪৭ সালে, সে দেশটির মামুলি এক নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য কেন লেগে গেল ২৩ বছর, সেটা বুঝতে হলে বাস্তব ইতিহাসের দিকে নজর ফেরাতে হয়, তাহলেই আন্দাজ করা যাবে কেন ভারত শাসন আইনের ধারাবাহিকতায় নির্বাচিত প্রতিনিধিরা গঠন করলেন পাকিস্তান গণপরিষদ এবং শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করতে লাগল নয় বছর। অধিকন্তু, সেই শাসনতন্ত্র অনুযায়ী সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের আগেভাগে ১৯৫৮ সালে জারি হলো সামরিক আইন। সাধারণ নির্বাচনকে এভাবে তোলা হয়েছিল শিকেয় এবং বুনিয়াদি গণতন্ত্র নামে নিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থা চালু করেও শেষ রক্ষা তাদের হয়নি। জনরোষে বিদায় নিতে হয়েছে এশিয়ার লৌহমানব জেনারেল আইয়ুব খানকে, আরেক জেনারেল ইয়াহিয়া খানকে ক্ষমতা হাতে নিতে হলো নির্বাচনের দৃঢ় অঙ্গীকার ব্যক্ত করে।
রাজনীতির এই পথপরিক্রমণ যত সহজে বলা গেল, প্রকৃত বাস্তবতা তত সরল ও শান্তিপূর্ণ ছিল না। সংকটের গোড়ায় ছিল পাকিস্তানের উভয় অংশের রাজনৈতিক, অথনৈতিক, সাংস্কৃতিক বাস্তবতার পার্থক্য। শাসনক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হয়েছিল পশ্চিমে, অন্যদিকে শিক্ষা-সংস্কৃতি, অর্থনীতি-রাজনীতিতে এগিয়ে ছিল পূর্ব বাংলা। আমলাতন্ত্র ও সামরিক বাহিনীতে ছিল পশ্চিমাদের আধিপত্য, অঞ্চলজুড়ে বড় ভূস্বামীদের দাপট, যাদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছিল উত্তর ভারত থেকে আসা মোহাজের ব্যবসায়ী ও শিল্পপতি। অন্যদিকে পূর্ব বাংলায় ছিল মধ্যবিত্তনির্ভর সমাজ, উদারমনা সংস্কৃতির পীঠস্থান, যেখানে পাকিস্তানের জনসংখ্যার ৫৬ শতাংশের বসবাস। এ সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল ছিল পাট, চা, চামড়ার কল্যাণে পাকিস্তানের বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের প্রধান উৎস। রাষ্ট্রের ওপর পশ্চিমা আধিপত্যের ফলে পূর্বের সম্পদ চালান হয়ে যেত পশ্চিমে এবং কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিমাঞ্চল উন্নত করতে নিয়োগ করে শক্তি ও সম্পদের বড় অংশ।
জাতীয় সত্তা সমুন্নত রেখে পাকিস্তানের শাসনক্ষমতায় বাঙালির অধিকার প্রতিষ্ঠার যে দীর্ঘ সংগ্রাম, সেখানে আপস-রফা মেনে নিয়েছেন কেউ কেউ, পথভ্রষ্ট হয়েছেন অনেকে, হয়েছেন পশ্চিমাদের বশংবদ, আইয়ুব খানের অনুরক্ত। মোদ্দাকথা, ক্ষুদ্র স্বার্থের জন্য জলাঞ্জলি দিয়েছেন জাতির অধিকার। তবে নিরাপস একাগ্র সংগ্রাম পরিচালনা করেছেন শেখ মুজিব, নীতির ক্ষেত্রে তথা বাঙালিত্বের প্রশ্নে আপস নেই—এই ছিল তার আপ্তবাক্য।
পাকিস্তানে সত্যিকার গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা পেলে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিসেবে বাঙালিরা পাবে প্রাধান্য, আর তাই সেটা ঠেকাতে নানা রকম দুর্বুদ্ধি খেলা করেছিল শাসকগোষ্ঠীর মনে। একপর্যায়ে তারা উত্থাপন করল সংখ্যা-সাম্যের ফর্মুলা, অর্থাৎ পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদে দুই অংশ থেকে সমান প্রতিনিধিত্ব থাকবে, পূর্ব ও পশ্চিম হচ্ছে পাকিস্তানের দুই ইউনিট, আর তাই ৩০০ আসনের পরিষদে ১৫০ আসন রইবে পশ্চিমের, ১৫০ পূর্বের। তার অর্থ এক ব্যক্তি এক ভোটের ভিত্তিতে নির্বাচন হবে না, হবে দুই প্রদেশে দুই সংখ্যানুসারে। পশ্চিম পাকিস্তান যেহেতু হবে এক ইউনিট, সেজন্য চারটি প্রদেশ বিলুপ্ত করে গোটা পশ্চিম পাকিস্তানকে একটি প্রদেশ হিসেবে গণ্য করা হলো। ফলে পাঞ্জাব, সিন্ধু, সীমান্ত প্রদেশ ও বেলুচিস্তান তাদের প্রাদেশিক অস্তিত্ব হারাল, আর পূর্ব বাংলা হারাল তার সংখ্যাগরিষ্ঠতার শক্তি। বঙ্গবন্ধুর দীক্ষাগুরু হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী মনে করেছিলেন এমন আপসরফা না করলে পাকিস্তানে কোনো দিন গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা পাবে না, আর তাই আইনমন্ত্রী হিসেবে এই আপস ফর্মুলার ভিত্তিতে তিনি ১৯৫৬ সালে পাকিস্তানকে একটি শাসনতন্ত্র উপহার দিতে সক্ষম হন। এই ঐতিহাসিক আপসে সম্মত ছিলেন না শেখ মুজিব, সেজন্য লিডারের সঙ্গে দ্বিমত করতে দ্বিধা করেননি এবং গণপরিষদের সদস্য হিসেবে সংবিধানে স্বাক্ষরদান থেকে তিনি বিরত ছিলেন।
তার পরে অনেক জল গড়িয়ে গেছে বুড়িগঙ্গা নদী ও সিন্ধু নদ দিয়ে, গণতান্ত্রিক নির্বাচন রোধ করে ক্ষমতা দখল করলেন জেনারেল আইয়ুব, ছুড়ে ফেলে দিলেন শাসনতন্ত্র, কারারুদ্ধ করলেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক নেতাদের। আইয়ুবের জয়রথ প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়েছিল শেখ মুজিবের আন্দোলন সংগ্রামের কাছে। সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যুর পর আওয়ামী লীগের হাল ধরে তিনি দল কেবল পুনরুজ্জীবিত করলেন না, তাকে নবজন্ম দিলেন ছয় দফা দাবিনামা ঘোষণা করে। বাঙালির এই বাঁচার দাবি প্রকৃত অর্থে পাকিস্তানের রাজনীতিতে পশ্চিমা আধিপত্য মোচন করে বাঙালির স্ব-শাসন প্রতিষ্ঠার রূপরেখা। ছয় দফা ঘোষণার পর হুংকার দিয়ে উঠেছিলেন আইয়ুব খান, শেখ মুজিবকে শূলে চড়ানোর আয়োজন তিনি করেছিলেন তথাকথিত ষড়যন্ত্র মামলায় সামরিক আদালতে বিচারের ব্যবস্থা করে। জনশক্তির আন্দোলনে মুক্তি পেলেন শেখ মুজিব, তাকে বরণ করা হলো বঙ্গবন্ধুরূপে, আইয়ুবের তখতে তাউশ গড়াগড়ি খেল ধুলোয়। ১৯৬৯ সালের মার্চে নবপর্যায়ে যে সামরিক শাসন শুরু হলো, তা ছিল তুলনামূলকভাবে দুর্বল, গণতান্ত্রিক শক্তির কাছে দ্রুত নির্বাচনের ব্যবস্থা করতে অঙ্গীকারবদ্ধ ছিল সামরিক সরকার। আর তাই মুক্তি দেয়া হলো সব রাজবন্দিকে, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা স্বীকৃত হলো এবং বঙ্গবন্ধুর ‘এক ব্যক্তি এক ভোট’ নীতি স্বীকৃত হলো। এক ইউনিট নয়, পশ্চিম পাকিস্তান আবার চার ইউনিটে রূপান্তর হলো, অর্থাৎ চারটি প্রদেশে প্রাদেশিক সরকার প্রতিষ্ঠা পাবে, সর্বপাকিস্তান সংসদে সংখ্যার ভিত্তিতে নির্ধারিত হবে আসন। পাকিস্তান জাতীয় পরিষদে আসন সংখ্যা দাঁড়াল নিম্নরূপ: পূর্ব বাংলা ১৬২, পাঞ্জাব ৮২, সিন্ধু ২৭, সীমান্ত প্রদেশ ২৫ এবং বেলুচিস্তান ৪। মোট ৩০০।
উল্লিখিত পটভূমিকায় নির্বাচনী কার্যক্রমের শুরুতে দূরদর্শী কর্তৃক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব। তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন তার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ এককভাবে নির্বাচনে লড়াই করবে। যেকোনো গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচনে সাধারণত রাজনৈতিক দল মিত্র খোঁজে, ভোটের বাক্স ভারী করার জন্য সমমনা অন্যান্য রাজনৈতিক দলের সঙ্গে ঐক্য গড়ে সম্মিলিতভাবে লড়াই করা অনেক সুবিধাজনক বিবেচিত হয়। ১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক নির্বাচনে দোর্দণ্ড প্রতাপ মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে যুক্তফ্রন্টের বিজয় তো ঐক্যের কারণেই সম্ভব হয়েছিল। আইয়ুব সরকারবিরোধী আন্দোলনও আওয়ামী লীগ ঐক্যবদ্ধভাবে করছিল, কিন্তু ১৯৬৬ সালে ছয় দফা ঘোষণার পর শেখ মুজিব গুরুত্বারোপ করেছিলেন একলা চলার ওপর। ছাত্রসমাজের ঐক্য ও রাজনৈতিক ঐক্যের তাত্পর্য উপলব্ধি করলেও নির্বাচনে কোনো ধরনের ঐক্য প্রয়াস তিনি নিলেন না। এ সিদ্ধান্ত গ্রহণের পেছনে যুক্তফ্রন্টের ব্যর্থতার তিক্ত স্মৃতি কাজ করেছিল, যখন এমন বিশাল বিজয়ের পর ষড়যন্ত্রের রাজনীতির কাছে নিজেদের বিকিয়ে দিয়ে চলল দলবদলের খেলা—পশ্চিম পাকিস্তানের ক্রীড়নক হতে রাজনীতিবিদদের মধ্যে হুড়োহুড়ি। অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু, সেই সঙ্গে বুঝতে পেরেছিলেন জনতার হূদস্পন্দন, তাই সিদ্ধান্ত নিলেন তার দল একাই লড়বে এবং তাকে নিশ্চিত করতে হবে পূর্ব পাকিস্তানের সব আসনে বিজয়। কারো কল্পনায় যা ছিল না, শেখ মুজিব যেন দিব্য চোখে তা দেখতে পেয়েছিলেন। তিনি বাছাই করলেন এমন প্রার্থী, যারা মানুষের আস্থার মর্যাদা রাখবেন, নীতির প্রশ্নে থাকবেন অটল। এদের অধিকাংশ এসেছেন মধ্যবিত্ত পেশাজীবী গোষ্ঠী থেকে, আর্থিক বিবেচনায় খুব সচ্ছল নন, তবে ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত।
অন্যদিকে পাকিস্তানি শাসকরাও তাদের প্রস্তুতি গ্রহণ করছিলেন। তাদের লক্ষ্য ছিল বাঙালির অধিকারকে কাটছাঁট করে একটা অনুমোদিত সীমার মধ্যে নিয়ে আসা। সেজন্য প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক হিসেবে জেনারেল ইয়াহিয়া খান জারি করলেন আইনগত কাঠামো আদেশ বা এলএফও। এ অধ্যাদেশবলে নির্বাচিত সংসদ এমন কোনো আইন প্রণয়ন করতে পারবেন না, যা রাষ্ট্রের ভিত্তি ইসলামী আদর্শ ক্ষুণ্ন করবে। ছোট-বড় ২০টি শর্ত উল্লিখিত হয় এলএফওতে। এ রকম শর্ত মেনে নির্বাচনে যাওয়া উচিত হবে কিনা, সে প্রশ্ন অনেকে তুলেছিলেন, কিন্তু বঙ্গবন্ধু এলএফওকে তেমন গুরুত্ব দেননি। তিনি সাংবিধানিক পথে বাঙালির অধিকার অর্জনের উপায় দেখতে পেয়েছিলেন নির্বাচনের মধ্যে। অন্যদিকে পাকিস্তানি শাসক চক্র নির্বাচন দিতে বাধ্য হয়েছিল, তবে তারা নিশ্চিত ছিল নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তানের আসন ভাগাভাগি হয়ে যাবে বিভিন্ন দলের মধ্যে। দক্ষিণপন্থী মুসলিম লীগ, নরমপন্থী পিডিপি এবং ধর্মীয় দল জামায়াতে ইসলামী, নেজামে ইসলামী পাবে বেশকিছু আসন। ফলে শাসকগোষ্ঠী রাজনীতিবিদদের নিয়ে খেলতে পারবে আগের মতো, পোষ মানা গণতন্ত্র সামলাতে পারবে তারা। মেজর জেনারেল ফজল মুকিম খান তার ‘পাকিস্তানস ক্রাইসিস ইন লিডারশিপ’ গ্রন্থে লিখেছিলেন, ‘১৯৭০ সালের আগস্ট নাগাদ সরকারের ধারণা ছিল আশু নির্বাচনের ফলাফল হবে নিম্নরূপ, জাতীয় পরিষদে পূর্ব পাকিস্তানের ১৬৭ আসনের মধ্যে শেখ মুজিবের আওয়ামী লীগ পাবে ৪৬ আসন, বড়জোর ৬০ থেকে ৭০ আসন।’ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের সংবিধানবিষয়ক উপদেষ্টা জি. ডব্লিউ. চৌধুরী সেপ্টেম্বরে লন্ডনে পাকিস্তান সোসাইটিতে প্রদত্ত ভাষণে বলেছিলেন, পূর্ব বা পশ্চিম পাকিস্তানে কোনো এক পার্টি সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করবে, সে রকম সম্ভাবনা নেই।
কিন্তু পাকিস্তানিদের সব হিসাব পাল্টে দিলেন শেখ মুজিবুর রহমান, তার নেতৃত্বে বাঙালিরা বিশ্বের নির্বাচনী ইতিহাসে অভাবিত ও অভূতপূর্ব বিজয় অর্জন করল, পূর্ব পাকিস্তানের ১৬২ নির্বাচনী আসনের ১৬০টিতে বিজয়ী হলো আওয়ামী লীগ, সংরক্ষিত নারী আসনসহ ৩১৩ আসনের পাকিস্তান জাতীয় পরিষদে তাদের আসন সংখ্যা দাঁড়াল ১৬৭। জাতীয় পরিষদে ছয় দফাভিত্তিক শাসনতন্ত্র প্রণয়নে নির্বাচনী ম্যান্ডেট ও সাংবিধানিক শক্তি তারা অর্জন করল।
জেনারেল ইয়াহিয়া খানের সামরিক শাসন তুলনামূলকভাবে ছিল দুর্বল। জনসমর্থন তাদের প্রতি ছিল না, তবে নির্বাচন অনুষ্ঠানে তাদের অঙ্গীকারে মানুষ আস্থা রেখেছিল। প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক ইয়াহিয়া খান নিজেও ছিলেন আমোদপ্রিয় দুর্বলচিত্তের মানুষ। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সামরিক শাসকদের কাছ থেকে দূরত্ব বজায় রেখে চলতেন, তবে প্রয়োজনে সমালোচনামুখর হতে দ্বিধা করতেন না। এলএফও নিয়ে তিনি সরব হননি, অন্যদিকে সত্তরের নভেম্বরে প্রবল ঘূর্ণিঝড়ে বিধ্বস্ত উপকূল অঞ্চলে সরকারের ত্রাণ পরিচালনায় ব্যর্থতা ও ইয়াহিয়া খানের অসংবেদনশীলতার তিনি ছিলেন তীব্র সমালোচক। নির্বাচন অনুষ্ঠানই ছিল বঙ্গবন্ধুর মূল লক্ষ্য, সেই নির্বাচন শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হয়েছিল এবং রাতারাতি পাল্টে দিয়েছিল পাকিস্তানের ক্ষমতার বিন্যাস। পশ্চিমা শাসকদের মর্জিমাফিক রাজনীতির গতিপ্রকৃতি আর ধার্য হবে না, জনগণের ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটবে রাজনীতিতে, সেভাবেই গড়ে উঠবে ক্ষমতার নতুন বিন্যাস। তবে আগামীতে আর যা-ই ঘটুক না কেন জনগণের ক্ষমতার সাংবিধানিক প্রকাশ অর্জন করল। আগামীর যেকোনো সমীকরণে বাঙালির অধিকার মুছে ফেলার উপায় কারো রইল না, আর বাঙালির হয়ে কথা বলার নিরঙ্কুশ অধিকার শেখ মুজিবের ওপর অর্পিত হলো। ইতিহাস তিনি নির্মাণ করলেন, আর ইতিহাস তাকে দিল এই কর্তৃত্ব। পরের ঘটনাধারা হোক যত কণ্টকময় ও বিপত্সংকুল, বাঙালির অগ্রযাত্রা হয়ে উঠছে অপ্রতিরোধ্য, নির্বাচনী গণরায় প্রতিষ্ঠা করল সেই সত্য, যার রূপকার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান; মানুষের সঙ্গে তার সম্পৃক্তি ও দীর্ঘ সংগ্রামের অভিজ্ঞতায় পুষ্ট যে নেতা অসাধারণ প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতা নিয়ে প্রতিষ্ঠা করলেন সাংবিধানিক কর্তৃত্ব। এখানে নিহিত সত্তরের নির্বাচনের মহান তাত্পর্য।
।।।
সংগৃহীত